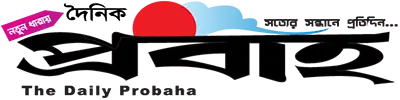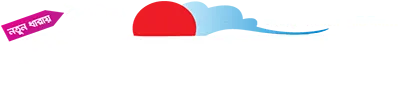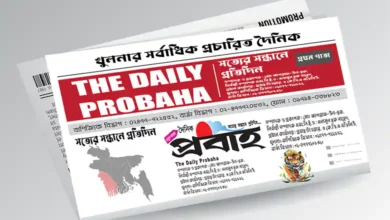ইউরোপের শ্রমবাজারে বাংলাদেশ: সম্ভাবনার চেয়ে সংকটই বড় বাস্তবতা
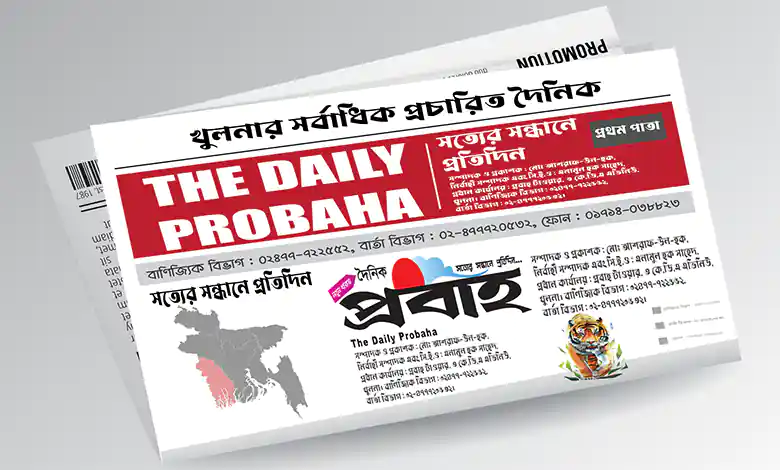
বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের প্রবাহ মূলত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমান বৈশি^ক প্রেক্ষাপটে ইউরোপের শ্রমবাজার ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখানেই প্রশ্ন-এই নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও কেন বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে প্রত্যাশিত হারে শ্রমিক পাঠাতে পারছে না? সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন। কিন্তু ইউরোপগামী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১৬ হাজারের কিছু বেশি-গত বছরের তুলনায় যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এর পেছনের বড় কারণ দক্ষতার অভাব, ভাষাগত দুর্বলতা এবং আন্তর্জাতিক মানদ-ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি। যেখানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ইউরোপের বাজারে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো সংগ্রামী। এখানে কেবল দক্ষতার অভাব নয়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির দুর্বলতাও স্পষ্ট। দেশে ১১০টি টিটিসি থাকলেও সেখানে দেওয়া প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী নয় বলে অভিমত বিশ্লেষকদের। বিএমইটির তথ্যমতে, পাঁচ বছরে প্রশিক্ষিত প্রায় ৪ লাখ কর্মীর মধ্যে মাত্র ৮-১২ শতাংশ বিদেশে যেতে পেরেছেন। বাকিরা দেশে কর্মহীন অবস্থায় হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন। এমন চিত্র আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের কাঠামোগত ত্রুটির প্রতিচ্ছবি। এছাড়া, ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ যে পর্যাপ্ত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা গড়তে পারেনি, সেটিও বড় অন্তরায়। দক্ষিণ ইউরোপের কিছু দেশের সঙ্গে আলোচনা চললেও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে এখনো কার্যকর কোনো চুক্তি গড়ে ওঠেনি। এই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হলে কূটনৈতিকভাবে আরও সক্রিয় হতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি কর্মীদের ইমেজ সংকট ও অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন প্রবণতাও ইউরোপীয় নিয়োগকর্তাদের আস্থা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হলো-এই সংকট নিরসনে করণীয় কী? এক্ষেত্রে টিটিসি ও বিএমইটি’র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা জরুরি। আন্তর্জাতিক মানদ-ে প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ প্রশিক্ষক ও বাজারমুখী কোর্স কারিকুলাম। প্রয়োজনে বিদেশি ট্রেইনার নিয়োগ ও বেসরকারি খাতে সহযোগিতা বাড়ানো উচিত। এছাড়াও ভাষাগত প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি রিক্রুটিং এজেন্সি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন সময়ের দাবি। এই দুটি সংস্থা নিজেদের আলাদা সত্তা হিসেবে না দেখে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে শ্রমিকদের বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জন সহজ হবে। ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে অধিক সংখ্যক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা দরকার, যাতে নিয়মিত, নিরাপদ ও আইনসম্মত অভিবাসনের পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা, তরুণ জনবল এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের আগ্রহ থাকলেও তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে সম্ভাবনা শুধু পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকবে। একুশ শতকে অভিবাসন কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এটি দক্ষতা, মর্যাদা এবং কৌশলের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে এখনই প্রস্তুত হতে হবে।