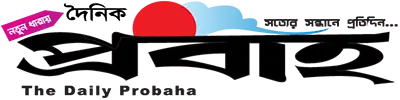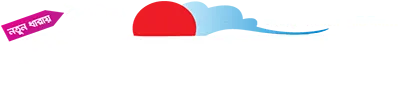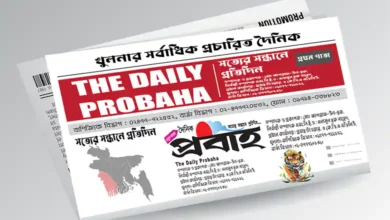নবায়নযোগ্য রূপান্তরের পথে হাঁটতে হবে
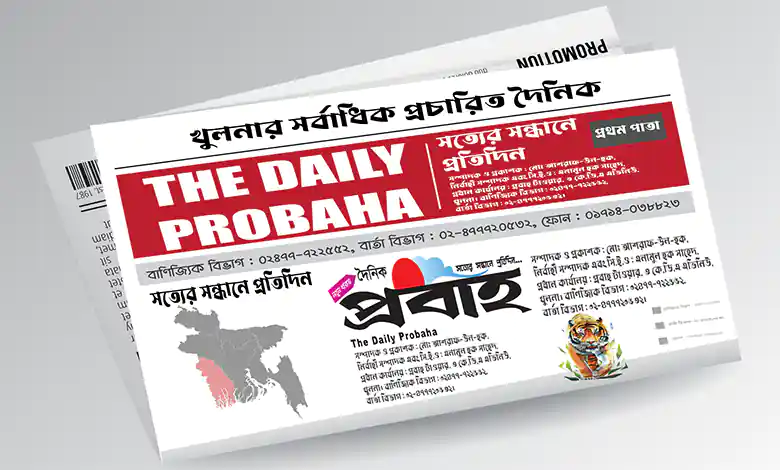
এলএনজি নির্ভরতায় বাড়ছে ঝুঁকি
বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) সর্বশেষ সতর্কবার্তা নিছক পরিসংখ্যান নয়, বরং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকটের এক স্পষ্ট পূর্বাভাস। একসময় দেশীয় গ্যাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ আজ মোট চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ আমদানি করছে। এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, আগামী এক দশকে এলএনজি আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা শুধু জ্বালানি খাত নয়, গোটা অর্থনীতিকেই দুর্বল করে তুলবে। এলএনজি আমদানির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না- দেশীয় গ্যাসের ঘাটতি মেটাতে এটি কার্যকর বিকল্প। কিন্তু উচ্চমূল্য, সীমিত অবকাঠামো এবং ঘনঘন ঘূর্ণিঝড়ের অভিঘাত এই খাতকে অস্থির করে তুলছে। ২০২৩ সালের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় টার্মিনাল বন্ধ হয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে উপকূলীয় স্থাপনাগুলো কতটা অরক্ষিত। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ না বাড়ালে ভবিষ্যতে একই সংকট আরও ঘন ঘন দেখা দিতে পারে। আইইএ’র প্রতিবেদনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বায়ুদূষণ। ২০২৪ সালে প্রতিদিন বিশ্বে ১৬ হাজারের বেশি মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে দূষণের কারণে। দক্ষিণ এশিয়ায় এর ক্ষতি জিডিপির ১১ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প খাতে কিছু উদ্যোগ নিলেও টেকসই সমাধান হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর। কানাডা ও চীনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, কয়লা বিদ্যুৎ বন্ধের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বায়ু মান নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়। বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুৎ প্রবেশাধিকার অর্জন করলেও লাখো পরিবার এখনো কাঠ বা গোবরের মতো ঐতিহ্যবাহী জ্বালানিতে রান্না করে। এর ফলে ঘরের ভেতরের দূষণ বাড়ছে। আইইএর অনুমান, সরকার যদি শেষ প্রান্তের সংযোগে বিনিয়োগ করে এবং বৈদ্যুতিক চুলার মতো সাশ্রয়ী বিকল্প সহজলভ্য করে, তবে ২০৩৩ সালের মধ্যে পরিষ্কার রান্নার জ্বালানির সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। এশিয়ায় এলএনজির দাম আগামী দশকে কমতে পারে, যা চাহিদা বাড়াবে। কিন্তু অবকাঠামো সংকট ও অর্থায়নের ঘাটতি এই প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করবে। একই সঙ্গে বিশ্ব এখনো ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমা রক্ষা করতে ব্যর্থ। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রেকর্ড বিনিয়োগ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েছে, কিন্তু বাস্তব অগ্রগতি ধীর। এখন জরুরি হলো বৈদেশিক ঋণ ও আমদানি নির্ভরতা না বাড়িয়ে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ দ্রুত সম্প্রসারণ। এতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও বায়ুদূষণ- দুই দিকেই উন্নতি সম্ভব। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধু জ্বালানির ধরন নয়, বরং জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতার ওপরও। প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে জ্বালানি আমদানি ও জলবায়ু অভিযোজনের পেছনে। এই দ্বিমুখী চাপ অর্থনীতিকে ক্রমাগত ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য বার্তাটি স্পষ্ট: জ্বালানি নীতি এখন আর কেবল সরবরাহের প্রশ্ন নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীলতার প্রশ্ন। এলএনজি নির্ভরতার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়াই দেশের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার একমাত্র পথ।