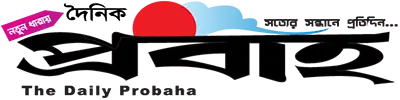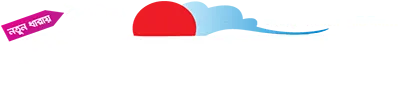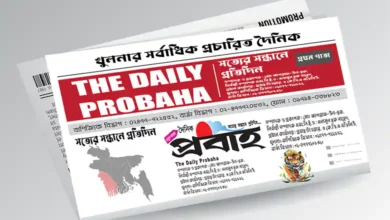মর্যাদা, দায়িত্ব ও সহানুভূতিভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামো চান মাহফুজ
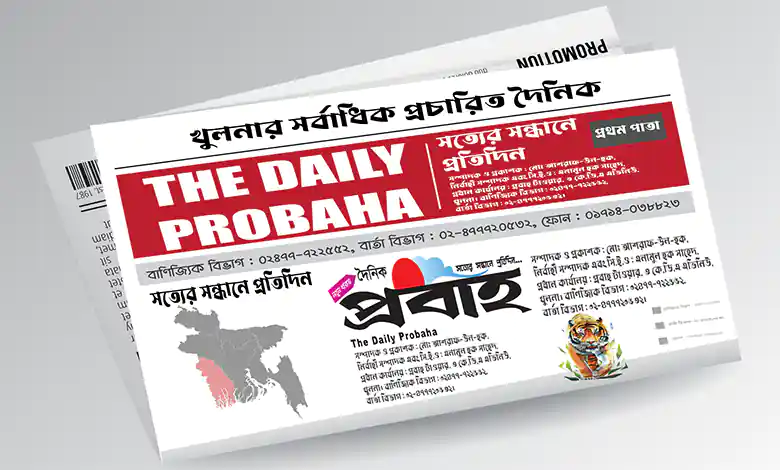
দ্য ডিপ্লোম্যাটকে সাক্ষাৎকার
প্রবাহ রিপোর্ট : বর্তমানে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রয়েছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিটিতেও। আমরা মর্যাদা, দায়িত্ব ও সহানুভূতির ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চাই। আমরা আবুল হাসেম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বোস ও চিত্তরঞ্জন দাসের মতো ব্যক্তিত্বদেরও শ্রদ্ধা করি। আমরা যে ধরনের নতুন সংবিধান চাই সেটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিভাজনমূলক নয়। আমরা সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির পাশাপাশি জন কূটনীতিকেও অগ্রাধিকার দিই। সম্প্রতি এশিয়া-প্যাসিফিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন দ্য ডিপ্লোম্যাটকে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ভবিষ্যত লক্ষ্য ও একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য চলমান আলোচনা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দিল্লির সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রিসার্চ স্কলার শাহাদাত হোসাইন। সাক্ষাতকারে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, দায়িত্ব ও সহানুভূতির রাজনীতির কথা বলেন তিনি। এর মানে কি। জবাবে মাহফুজ আলম বলেন, গত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের নিপীড়নমূলক রাজনীতির কারণে মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অধিকারের দাবি তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। যদিও আমি মনে করি, অধিকার দায়িত্বের সঙ্গেই আসে। আমাদের এককভাবে অধিকারভিত্তিক রাজনীতি থেকে দায়িত্বভিত্তিক রাজনীতির দিকে যেতে হবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা জনগণের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভাজন তৈরি করে এমন ফ্যাসিবাদী রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বোঝাপড়ার রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জন্য মর্যাদা, দায়িত্ব ও সহানুভূতিশীল মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক কাঠামো চাই। আমরা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে চাই। আমাদের অবশ্যই মুজিববাদের মতো সংঘাতময় রাজনীতির বাইরে যেতে হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে হবে। সহানুভূতি ছাড়া মানুষের সঙ্গে সংযোগ বা প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি অর্জন অসম্ভব। আর ঠিক এই কারণেই আমরা সহানুভূতি ও দায়িত্বকেন্দ্রিক রাজনীতির পক্ষে কথা বলি।
প্রশ্ন: আপনি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ঢাকা হবে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই যুক্তির ভিত্তি জানতে চাইলে মাহফুজ আলম বলেন, বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বাংলা। ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম যোগ পাঠের অনুবাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলে এসেছে। এই ভূমি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদিদের আবাসস্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাকে আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলনস্থল হিসেবে দেখি, যেটির কেন্দ্রে ছিল ঢাকা। বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস এখানে মিশে গেছে। যারফলে মানুষের মধ্যে মতামত, বিশ্বাস ও ধারণায় বৈচিত্র্যতা এসেছে। এই ভূমি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণে সমৃদ্ধ হওয়ায় কোনও একক মতাদর্শ এখানে আধিপত্য দেখাতে পারেনি। এই ভূমি এমন এক সমৃদ্ধ ভূমি যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও বৈষ্ণবরা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সহাবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করেছে। এখানে বঙ্গোপসাগরের পরিচয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরের চারপাশে চট্টগ্রাম, আরাকান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের অবস্থান যেখানে গত ২০০-৩০০ বছর ধরে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটছে। আমরা চাই বাংলাদেশ এই অতীত উত্তরাধিকারকে ধারণ করুক এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যময় ধারণার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হোক।
প্রশ্ন: আপনি ৪৭ (ভারত ভাগ), ৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ) এবং ২৪ (জুলাই বিপ্লব) এর চেতনাকে একত্রিত করা উচিত বলে মনে করছেন। তবে প্রতিটি ঘটনার একটি আলাদা চেতনা ছিল। এই তিনটি ঘটনাকে কীভাবে একত্রিত করা যায় জানতে চাইলে মাহফুজ আলম বলেন, আমি মনে করি, ১৯৪৭ ও ১৯৭১ এর চেতনার মধ্যে একটি মিল ছিল, যেটির ভিত্তিতে বাঙালি মুসলমানরা সম্মিলিত পদক্ষেপ নিয়েছিল। নিজেদের সম্মিলিত লক্ষ্যগুলোর মূল আকাঙ্ক্ষার কারণেই ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে তারা হিন্দু ও অন্যদের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল। যদিও ১৯৪৭ সালের আন্দোলনটি মুসলিম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল, তবে পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনে নি¤œবর্ণের হিন্দুদেরও ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৭১ সালেও হিন্দু বন্ধুদের পাশাপাশি একই উদ্দেশে বাঙালি মুসলমানরাও লড়েছিল। ১৯৪৭ সালের লক্ষ্য ছিল, একটি স্বদেশ খোঁজা তারা যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে, জমিদারি প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি চর্চা করতে পারবে। তবে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা নয়, ধর্মীয় স্বাধীনতাই ছিল ওই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পরে অবশ্য কিছু ইসলামি প-িত এই দিকটিকে অতিরঞ্জিত করে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করেছে। আমি বরং মনে করি, পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধু ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ। ১৯৪৭ সালের আগে এ অঞ্চলে এই ধরনের স্বাধীনতা সীমিত পরিসরে ছিল। তখন সমগ্র বাংলা কেন পাকিস্তানের সঙ্গে মিশেনি? পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও শ্রেণিগত বিভাজন ছিল যেটির ইন্ধন যোগান শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী। বাঙালি মুসলমানরা একটি অখ- বাংলাকে সমর্থন করেছিল যেটিকে আমরা এখনও সমর্থন করি। আমরা আবুল হাশেমের মতো গুরুদের শ্রদ্ধা করি, যিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে অখ- বাংলা চেয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও বাঙালি পরিচয়ের প্রয়াসে বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে অখ- বাংলার পক্ষে কথা বলেন। চিত্তরঞ্জন দাসকে আমরা তার কাজের জন্যেই শ্রদ্ধা জানাই। ১৯৭১ সালের লড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে, বাঙালি মুসলমান বা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে নয়, সেটি ছিল রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশি পরিচয়ের সূচনা হয়। ১৯৪৭ না হলে ১৯৭১ও হতো না, যেমনটি আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে লাহোর প্রস্তাবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনকে আমি ভিন্নভাবে দেখি। আমি এটিকে পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন বলি। কেননা, এটি বাঙালিদের আন্দোলন ছিল। তারা যখন বুঝতে পেরেছিলেন পাঞ্জাবি আধিপত্যের কারণে রাষ্ট্রে কার্যকর স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তরিত হয়নি, ১৯৭১ সালে তখন এই নিয়ন্ত্রণকে উচ্ছেদ করেন তারা। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল সমতার আহ্বান, যেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ বৈষম্যের বিরোধিতা করে ও সমান সুযোগের আশায় একসঙ্গে রাস্তায় নামে। এতে মাদ্রাসার ছাত্রসহ ইসলামিক স্কলাররা অংশ নেন ও প্রায় ১০০ মাদ্রাসা ছাত্র শহীদ হন। ১৫ বছর ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তারা। যারা ধর্ম পালন করে তাদের জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক ও নারীরাও লড়াই করেছেন। প্রতিটি শ্রেণির নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত ছিল। এসব পার্থক্য সত্ত্বেও সম্মিলিত শুরুর মূলকেন্দ্র ছিল বৈষম্যের বিরোধিতা ও সমতার অন্বেষণ। তাই আমরা এই সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর কাজ করে যাব। সাক্ষাতকারগ্রহীতা প্রশ্ন করেন, তাহলে বাংলাদেশের চূড়ান্ত ভিত্তি কী? এ অঞ্চলের মানুষ যখন ধারাবাহিকভাবে লড়াই করছে, তখন মানুষ বা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিচয় কী? জবাবে মাহফুজ আলম বলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের ঐক্যের মধ্যেই বাংলাদেশের ভিত্তি নিহিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের রাজনীতির প্রয়োজন নেই। সাধারণত তারাই রাষ্ট্রের আকৃতি স্পষ্ট করে। রাষ্ট্রের দুটি দিক: রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিকাশ এবং রাষ্ট্র গঠন। বাঙালি মুসলিম আকাঙ্ক্ষা থেকেই রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে। রাষ্ট্রকে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু সবাইকে সমান বিবেচনা করতে হবে। অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি মুসলমানদের বারবার সংগ্রাম করেছে। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবি আধিপত্যের কারণে সেটি তারা অর্জন করতে পারেনি। আর ১৯৭১ সালে মুজিববাদ তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল। এমন একটি রাষ্ট্র যেটি একইসঙ্গে বৈষম্যহীন, আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও আরও বেশি সমতার, তেমন একটি রাষ্ট্রের সন্ধানে ২০২৪ সালে আবারও তারা জেগে ওঠেছে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থাকা সত্ত্বেও এই লড়াই ধর্মের নয়, ধর্মীয় শাসনের জন্য নয়, সাম্য ও ন্যায়বিচারের জন্য।